X


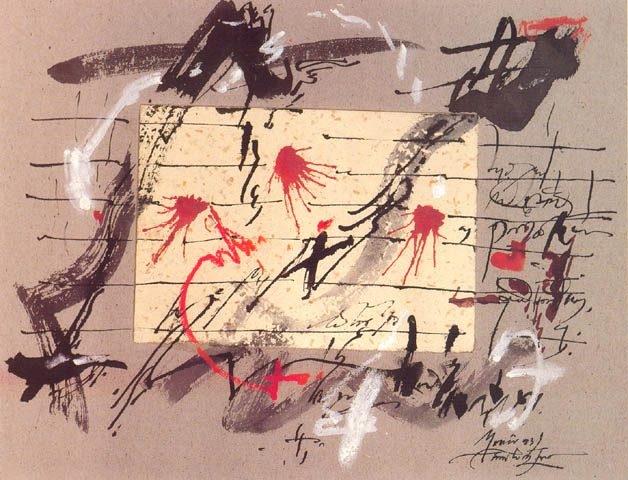
পাভেল আখতার: শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজের একটি অংশের মধ্যে যে প্রবণতাটি ক্রমবর্ধমান তা হ’ল, সমাজের অ-শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, প্রান্তিক মানুষদের বৌদ্ধিক সমালোচনার সুরকে উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়া । সমাজের অ-শীলিত সেই অংশটি যাপনে অত্যন্ত সহজ এই অর্থে যে, তাদের হাসিকান্না, রাগ, দুঃখ, অভিমান, উত্তেজনা, বিষাদ, আনন্দ সবই একেবারে অকৃত্রিম, অবাধ ও উন্মুক্ত । বুদ্ধির দীপ্তি দিয়ে, বোধের স্ফুরণ দিয়ে, চিন্তার শিল্পকলা দিয়ে জীবনের অভিব্যক্তিগুলিকে নাগরিক পোশাক পরিয়ে মেপে প্রকাশ করতেই তারা শেখেনি । তাদের কাছ থেকে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজ যা ‘প্রত্যাশা’ করে তার বাস্তব বিচ্ছুরণের জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের পাশে থাকা, তাদের কাছে থাকা, কাছে যাওয়া । তাদের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করা । এই অত্যন্ত জরুরি কাজটা থেকে বিস্তর দূরে থেকে, দূরত্ব রচনা করে, আবার তাদেরই কিছু কিছু ‘আচরণ’ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করা, অথবা দুরন্ত সমালোচনার ঝড় তোলা, এর মধ্যে নিদারুণ নির্মমতা ছাড়া আর কিছু নেই । রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি’ । কথাটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা বোঝার চেষ্টা হলে ‘অমন’ বিসদৃশ বৌদ্ধিক বিভ্রান্তিপূর্ণ ‘ব্যবহার’ দৃষ্টিগোচর হ’ত না । ‘স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে’ । ‘বৃহৎ জগৎ’ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এক ধরনের পলায়নীবৃত্তি । এই জীবনচর্যার অনুশীলনমগ্ন, শিক্ষার গৌরবদীপ্ত মানুষের পক্ষে ‘বৃহৎ সমাজের’ সমালোচনা অনধিকারচর্চাও বটে । যাদের বোঝারই চেষ্টা হ’ল না, যাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা হ’ল, তাদের সম্পর্কে ‘বিশ্লেষণ’ও যে সম্যক ভুলে ভরা হবে, সেটাও তো সন্দেহাতীত সত্য ।
এটা বাস্তব যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে নিম্নবিত্ত সমাজের একটা মানসিক দূরত্ব আছে । দূরত্বটা মেলামেশার অভাব থেকে সৃষ্ট । এর ফলে নিম্নবিত্ত, সাধারণ মানুষের ‘মন পড়ায়’ তাদের অক্ষমতা তৈরি হয় । একটি উদাহরণ দেওয়া যাক । সরকারি যেসব সাহায্য বা সুবিধা নিম্নবিত্ত, সাধারণ মানুষ পায় সেসব কিন্তু একটি জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থায় তাদের পাওয়ারই কথা । ভোট-রাজনীতির জন্য সেসব দেওয়া হোক অথবা না হোক, সেই আরামপ্রিয় চর্চাটা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের । তারা কিন্তু সেটা ভাবার বিলাসিতা দেখাতে পারে না । কারণ, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা অবস্থান । এবং, সেই সাপেক্ষেই ‘প্রাপ্তি’ যত যৎসামান্যই হোক না কেন তা তাদের কাছে অনেক । এই নিরিখে তাদের সহজলভ্য প্রাপ্তিগুলিকে সস্তা রাজনীতির উপহার বলে চিহ্নিত করলে তা যেমন ধোপে টেকার কথা নয়, তেমনই সেজন্য সমালোচক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকেও তারা ‘আপন’ ভাবতে পারবে না । উপরন্তু, দূরত্বটা আরও বাড়বে । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের আরেকটি ভুল অভিব্যক্তি হ’ল, ‘খয়রাতি’র সঙ্গে চাকরিতে নিয়োগে গড়িমসি, মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে সরকারি অনীহা ইত্যাদি বিষয়গুলিকেও জড়িয়ে একাকার করে ফেলার প্রবণতা । অথচ, ‘খয়রাতি’র সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক আদতে নেই । নিছকই তাদের অনুমান এবং অন্তঃসলিলা রাগের সহজ কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যে নিম্নবিত্ত, সাধারণ মানুষের সমাজ তা যুক্তিসিদ্ধ যেমন নয়, তেমনই মানবিকতাবর্জিতও । এতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্ত, সাধারণ মানুষের সমাজের ‘দূরত্ব’ কমার বদলে আরও বাড়ার সম্ভাবনা বেশি।
আদতে ‘শিক্ষিত মধ্যবিত্ত’ সমাজের ভাববাদী আদর্শবোধ সাধারণ মানুষকে কতটা স্পর্শ করে তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে । ‘সাধারণ মানুষ’ বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ‘প্রান্তিক মানুষ’ নিত্যদিনের ‘চাওয়া-পাওয়া’কেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে । দ্বিতীয়ত, ‘সাধারণ মানুষ’ বলতে যে বৃহত্তর জনসমাজকে বোঝায় তাকে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখার অবকাশ নেই । সেখানে ‘অসন্তুষ্টি’ যেমন থাকে তেমনই কিন্তু ‘সন্তুষ্টি’ও থাকে । সাধারণত ‘খয়রাতি’ বলতে যা বোঝানো হয় তা আসলে ‘অনুদান’ । জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের (welfare state ) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ’ল, ‘অনুদান’ । এই আদর্শিক চিন্তাধারা ফেবিয়ান সমাজবাদীদের মস্তিষ্কপ্রসূত । এতদসত্ত্বেও প্রশ্ন হচ্ছে, ‘অনুদান’ বস্তুটা দীর্ঘমেয়াদি হওয়া কি কাম্য ? ‘অনুদান’-এর লক্ষ্য সাময়িক সংকট দূর করা । উল্লেখ্য, বৃহত্তর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তিভূমি ‘অনুদান’ নয় । যদি ক্রমাগত ‘অনুদান’ দেওয়া হতে থাকে তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথিত সাময়িক সংকট দূরীভূত হয়নি । কিন্তু, হয়নি বলে দেওয়া হচ্ছে একথার মধ্যে ‘রাজনৈতিক চতুরতা’ আছে । সেই চতুরতায় এই প্রশ্ন নিশ্চয় হারিয়ে যায় না যে, আসল বস্তু কি এই নয় যে, অনুদানের ভিত্তিতে সংকট দূর করার চেয়ে ব্যক্তি অথবা পরিবারকে তার প্রান্তিকতা মোচনে স্থায়ীভাবে ‘সক্ষম’ করে তোলা ? ঠিকই, এটা সমালোচনার অভিমুখ হতে পারে, প্রান্তিক মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের পরিবর্তে ।
শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জটিল মনস্তত্ত্ব ও নির্মম বাস্তবকে চলচ্চিত্রের পর্দায় উদ্ভাসিত করে আমাদের বিবেক ও চৈতন্যকে প্রশ্ন করার, যেন একটা স্বচ্ছ দর্পণ সামনে রেখে নিজের ছায়াকে মূর্ত করে তোলার পথিকৃৎ পরিচালক যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে তিনি মৃণাল সেন । ‘খারিজ’ ছবিতে মধ্যবিত্ত মানসিকতার যে সংকট ও জটিলতা ক্রমশ সঙ্কুচিত, ধূসর হয়ে আসা মানবিকবোধের পরিসরে উচ্চারিত হয়েছিল, সেটিই তাঁর সমগ্র চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকা কেন্দ্রীয় সুর । তাঁর ‘নীল আকাশের নীচে’ ছবিটির একটি বিষাদমধুর, সুখশ্রাব্য গান--’ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে...!’ সত্যি বলতে কি, জগৎ-সংসারে নদীর মতো ‘নীরব শ্রোতা’ যে বিরল ! মর্ত্যপৃথিবীর সমস্ত হৃদয়দ্বার হয়তো রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে ! আর্ত, বিপন্ন হৃদয়ের সমস্ত রক্তাক্ত ভাষা শোনার সময় ফুরিয়ে যেতে পারে ! কিন্তু নীরবে, শান্ত লয়ে বয়ে চলা নদী কখনও ‘ফিরিয়ে’ দেয় না ! সে শোনে নীরবে, যেন গভীর সহমর্মিতায় ! ‘আবিল হিসেবগুচ্ছের’ অনেক ঊর্ধ্বে যে তার অবস্থান ; যে ‘হিসেবী চর্যা’ মধ্যবিত্তের জীবনলক্ষণ !
বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র অভিনয় করেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘দহন’ ছবিতে । সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ছবিটিতে দেখা যায় যে, একটি ‘লাঞ্ছিতা’ মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় একক প্রতিরোধ গড়ে তোলে আরেকটি মেয়ে । এই ছবিতেও মধ্যবিত্ত সমাজমানস যে কীভাবে পচে গলে ‘দুর্গন্ধ’ ছড়াতে শুরু করেছে তার নিদর্শন হচ্ছে, একদিকে ‘লাঞ্ছিতা’ মেয়েটিকে, অন্যদিকে তার হয়ে একমাত্র ‘প্রতিবাদী’ মেয়েটিকেও তাদের পরিবারেই প্রশ্নের, ঘৃণার, অবহেলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ! ‘প্রতিবাদী’ মেয়েটিকে যখন তার পরিবারও ভুল বুঝছে, ‘অত সব ঝামেলায়’ না-জড়িয়ে আত্মপরতার খোলসে আবৃত থাকার ‘শুচিশুভ্র’ মধ্যবিত্ত মানসিকতার চর্যাটিকে গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে তখন এইসব দেখে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে ঝরে পড়ছে এই অবিস্মরণীয় আর্তনাদ, আত্মজিজ্ঞাসার ঢঙে : ‘অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করা স্বাভাবিক, না কি প্রতিবাদ না-করাটাই স্বাভাবিক, কিংবা অন্যায় হওয়াটাই স্বাভাবিক !’ ‘সংশয় তিমির মাঝে’ ব্যক্তির বিচলিত হওয়ার এই মুদ্রা যেন সমগ্রকে, সমষ্টিকে ছুঁতে পারে সেটাই বোধহয় ছবির পরিচালকের মূল অভিপ্রায় ছিল ! কিন্তু, কোন ধ্বস্ত সামাজিক পটভূমিতে এমন ‘গভীর সংশয়’ সুস্থ চেতনার মানুষকেও কুরে কুরে খেতে থাকে আর অন্তিমে তীব্র হয়ে ওঠে ‘জীবনবিতৃষ্ণা’ তা ভাবার বিষয় ! কেবল ‘সংশয়’ বললে অবশ্য ‘খণ্ড সত্য’ বলা হবে, আসলে তো ‘ধিক্কার’ ধ্বনিত হচ্ছে!
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে...।’ ব্যক্তির প্রতি অন্যায়ে ব্যক্তি কোন অবস্থান নেবে সেটা নিতান্তই মূর্ত । কিন্তু, যে ঘটমান বা পুরাঘটিত অন্যায় গোটা সমাজকে, সমাজব্যবস্থাকে খাদের কিনারে নিয়ে যেতে পারে, সে অন্যায়ের অভিঘাতটা যেহেতু অনাগত ও বিমূর্ত ভবিষ্যতের পটে আঁকা ও প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নয় সেহেতু একধরনের স্থবিরতা বা নিশ্চল মূর্তি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে । উপরন্তু, ‘অন্যায়’-এর ব্যাপ্তির নিরিখে দেখলে এই দৃশ্যও খুব সাধারণ যে, ঘৃণা, দ্রোহ, প্রতিবাদ ইত্যাদিও নানা ‘খোপে’ আবদ্ধ । এমন মানুষ একেবারেই বিরল যাকে সমস্ত ঘটমান অন্যায়েই ঘৃণা, দ্রোহ ও প্রতিবাদের মূর্তিতে দেখা যায় । এর কারণই হ’ল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসের জটিলতা ! এভাবেই কালের দর্পণে ‘প্রতিবাদ’ শব্দটি আর গরিমায় উদ্ভাসিত নয়, বরং কালিমায় অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে!
অগণিত ‘জঞ্জাল’ সরিয়ে পৃথিবীকে নবজাতকের জন্য ‘বাসযোগ্য’ করে যাওয়ার অঙ্গীকারের উচ্চারণ করেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য । মহার্ঘ সেই উচ্চারণ বা ঘোষণা--’ছোট’র উদ্দেশে ‘বড়’র । কিন্তু, ‘বড়’র মধ্যে যে পঙ্কিলতা পল্লবিত সে যদি তার শৈশবে বা ‘বড়’ হয়ে ওঠার দিনগুলিতে মানবতার পাঠ ঠিকমতো পেত, তাহলে কি ‘মানুষ’ হিসেবে নিজেই নিজের মৌলিক পরিচিতিটাকে নিরর্থক করতে ব্যগ্র হয়ে উঠত ? শিশু যখন বড় হচ্ছে আদরে ও সোহাগে, তখনই তার অন্তর্গত সত্তায় সঠিক মূল্যবোধের শিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবতার পাঠ সঞ্চারিত করে দেওয়া প্রয়োজন । শিশুকে ভাল খাদ্য, ভাল বস্ত্র বা আরও অনেক ‘ভাল’ কিছু দেওয়ার চেয়ে তার ‘উত্তম চরিত্র’ গঠন করা, তাকে ‘যথার্থ মানুষ’ করে গড়ে তোলা পিতামাতার দিক থেকে সবচেয়ে জরুরি একটি কাজ বা কর্তব্য । শুধু ‘বড়’ হলেই হয় না, ‘ছোট’-কে কীভাবে বড় করা হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করেই ‘বড়’র যথার্থ ‘বড়ত্ব’ প্রমাণিত হয় ।
কিন্তু, বাস্তবে ছোটদের কীভাবে বড় করা হচ্ছে তার অনুরণন পাওয়া যায় বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক কৃষণ চন্দর ( ১৯১৪--১৯৭৭ )-এর একটি অসামান্য গল্পে । গল্পটির নাম--’মানুষ’ ; যার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই---একজন রুগ্ন ও দুর্বল শ্রমিক একদিন রাত্রে শহরের রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে অসতর্কতায় রাস্তার ম্যানহোলে পড়ে যায় ! সারারাত অভুক্ত ও অনিদ্রিত অবস্থায় ওখানেই সে থাকে ! সকাল হলে তার আর্ত-বিপন্ন কণ্ঠস্বর শুনে একে একে এগিয়ে আসে পৌরসভার কর্মী, সাংবাদিক, পুলিশ, হবু বরের গৃহসন্ধানী লোকজন ইত্যাদি । সকলেই তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে, নিজের প্রয়োজনও মিটিয়ে নেয়, আবার সন্দেহ-ও প্রকাশ করে ইত্যাদি । কিন্তু, একবারের জন্যেও তাকে গর্ত থেকে উপরে তুলে আনার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না ! বেলা বাড়তে থাকে । ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বিকেলে একটি শিশু ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা ওই আর্তস্বর শুনে এগিয়ে যায় ম্যানহোলের দিকে, মায়ের হাত ছাড়িয়ে । শিশুটি তার কোমল ও ছোট্ট হাতদুটি বাড়িয়ে দেয় তাকে উপরে তোলার জন্য । কিন্তু, গর্ত অবধি তার হাত আর পৌঁছয় না ! মা ধমক দিয়ে শিশুটিকে টেনে নিয়ে যায় । তারপর সন্ধ্যা হয় এবং রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে । শ্রমিকের ততোধিক রুগ্ন ও দুর্বল স্ত্রী স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত শরীরে অবশেষে পৌঁছে যায় ওই অভিশপ্ত গর্তের কাছে । ক্রন্দনাতুর স্ত্রী প্রাণপণে তার হাতদুটি বাড়িয়ে স্বামীকে তুলতে গিয়ে শেষপর্যন্ত নিজেও পড়ে যায় সেই ম্যানহোলে ! গল্পটি এখানেই শেষ । শুধু পরিশেষে, গল্পকার অমোঘ ও অভূতপূর্ব একটি মোচড় রেখেছেন এভাবে যে, তারপর শ্রমিক-দম্পতি ওখানেই, ওই গর্তের মধ্যেই তার সংসার-জীবন অতিবাহিত করতে থাকে !
পুরোদস্তুর রূপক গল্পটি বহু বছর আগে লেখা হলেও, আজও অপরিবর্তিত আমাদের স্বার্থমগ্ন মধ্যবিত্ত সমাজের গালে এক কঠিন চপেটাঘাত ! শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ নিজের নিশ্ছিদ্র আত্মবিভোরতা ও আরামপ্রিয়তার খোলসে এমনভাবে ঢুকে থাকে যে, সেখানে ‘সংবেদনা’ বস্তুটির আলো ঠিকঠাক প্রবেশ করতে পারে না । যে ভ্রান্তিবহুল দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত কপট আদর্শবাদিতার ঝংকার তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তা আসলে নিছক বহিরাবরণ, অন্তরে অজস্র জটিলতাকে লালন করায় তা বড্ড ফাঁপা, অসার !!


All Rights Reserved © Copyright 2025 | Design & Developed by Webguys Direct